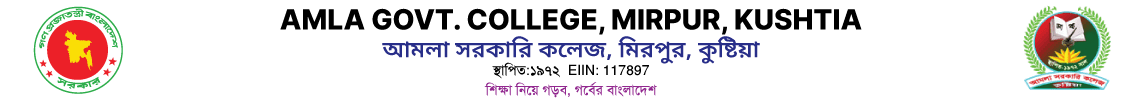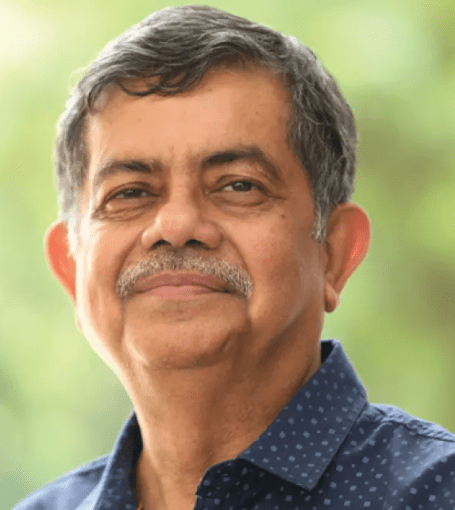কলেজের ইতিহাস
আমলা সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
আমলা সরকারি কলেজ কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী সরকারি কলেজ। এ কলেজটি মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নে অবস্থিত। এটি ১৯৭২ সালের ১ জুলাই উত্তর-দক্ষিণবঙ্গের বিখ্যাত কৃষক আন্দোলনের নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মারফত আলি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণ নিয়ে এ অঞ্চলের শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে জমিদারী বাড়ি এবং আমলা সদরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জমির কিছু অংশ নিয়ে এই কলেজটি স্থাপন করেন। পরবর্তিতে, আমলা হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এর এক ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৮৭ সালে ৩ নভেম্বর কলেজটিকে জাতীয়করণ করা হয়।
৬.৩ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি শুধুমাত্র আমলা’র জমিদারী’র-ই নয় বাংলার জমিদারী ইতিহাসের একটি বিশাল অংশ। জমিদার রামানন্দ সিংহ রায়ের প্রাসাদ যেটি ভগবান নিবাস নামে পরিচিত তা কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জমিদার কন্যা শ্যামা সুন্দরী দেবীর ৩ ছেলে ছিল যথা: সুরেন্দ্র নারায়ন সিংহ, সমোরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, ব্রজেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বা পাল (বিপিএিল)। ব্রজেন্দ্র নারায়ণ সিংহ’র প্রাসাদটি বর্তমানে কলেজের প্রশাসনিক ভবন হিসেবে এবং সুরেন্দ্র নারায়ন সিংহ’র বাসভবনটি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ডরমিটরি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সমোরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ’র বাসভবনটি কালের বিবর্তনে ধ্বংস হয়ে গেছে। তার কিছু অবশিষ্টাংশ দেখা যায়। জমিদার রামানন্দ সিংহ রায় তাঁর দুই কন্যার জন্য দুটি দিঘী খনন করেছিলেন এবং দুটোতেই শান বাঁধানো ঘাট ছিল। কলেজের বিজ্ঞান ভবনের দক্ষিণাংশে প্যারী সুন্দরী দেবীর ঘাটটি একটু দেখা গেলেও শ্যামা সুন্দরীর ঘাটটি সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। কলেজ ক্যাম্পাসের দিকে তাকালেই মনে হয় আমরা সেই জমিদারী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আজও আছি। সে সময়কার দৃষ্টিনন্দন ভবন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মনে উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে। আমলা সরকারি কলেজ যতদিন থাকবে, আমলার জমিদারীর ইতিহাসও বেঁচে থাকবে কালের সাক্ষী হয়ে।
তথ্য সূত্র:
১। বাংলা পিডিয়া, bn.banglapedia.org
২। কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, ঢাকা: খান পাবলিকেশন্স।
৩। কুমুদনাথ মল্লিক, বিলু কবীর (সম্পা.), নদীয়া কাহিনী, ঢাকা: বইপত্র।
৪। কমল চৌধুরী, বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা, কলকাতা: দ্বেজ পাবলিশিং।
২। কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, ঢাকা: খান পাবলিকেশন্স।
৩। কুমুদনাথ মল্লিক, বিলু কবীর (সম্পা.), নদীয়া কাহিনী, ঢাকা: বইপত্র।
৪। কমল চৌধুরী, বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা, কলকাতা: দ্বেজ পাবলিশিং।
৫। ড. নাজিম সুলতান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ।